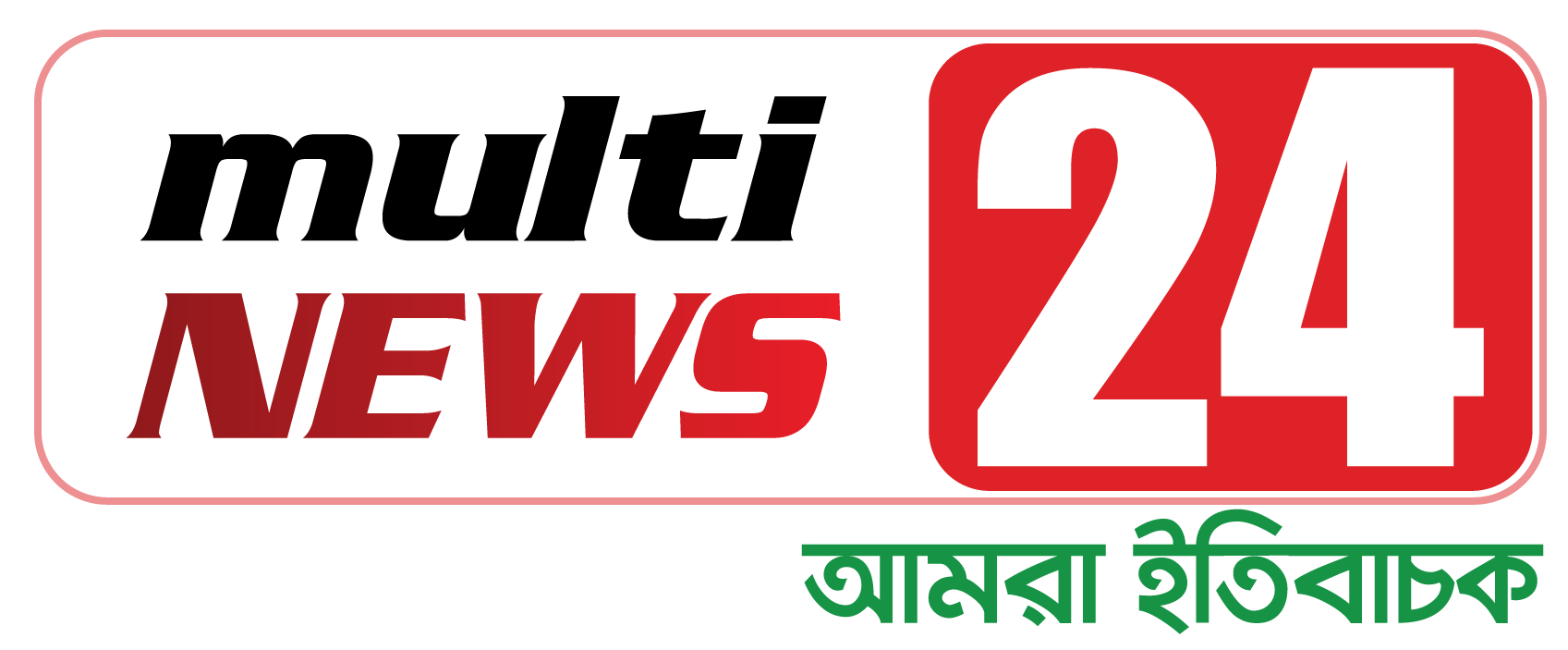আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥/ তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,/বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,/ কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।/ নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ-/সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥ (পূজা হতে সংগৃহীত)
রবীন্দ্রজীবনচরিত গভীরভাবে অনুশীলন করলে তার থেকে আমরা এমন কিছু শিক্ষা পেতে পারি, যা আমাদের বেঁচে থাকার পথকে আলোকিত করে তোলে। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-উৎসবে– এমন কী নিদারুণ ধ্বংসলীলার মধ্যেও তাঁর গান, তাঁর কবিতা মানুষের হৃদয়জুড়ে আছে এবং থাকবেও। একথা গভীর আত্মবিশ্বাসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন। চীন সফরে গিয়ে তিনি সে-কথা বলেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই বহুবার তা প্রত্যক্ষ করেছেন।
পৃথিবীর অন্যতম যুদ্ধবিরোধী কবি উইলফ্রিড ওয়েনকে (১৮ মার্চ ১৮৯৩-৪ নভেম্বর, ১৯১৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (২৮ জুলাই ১৯১৪-১১ নভেম্বর ১৯১৮) রণাঙ্গনে যেতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই, এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা হলো এই যে তাঁকে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে যুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র সাত দিন আগে নিহত হতে হয়েছিল। যুদ্ধে নিহত সেই মহান ইংরেজ কবির পকেটে পাওয়া গিয়েছিল একটি ডায়েরি, লেখা ছিল ১৯১২ সালে প্রকাশিত গীতাঞ্জলির ইংরেজি সং অফারিংসের ৯৬ সংখ্যক কবিতাটি।
কবিতার নিচে ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছিল। (অর্থাৎ ১৯১০ সালে ১৪ আগস্ট বাংলা ‘গীতাঞ্জলির…১৫৭ সংখ্যক কবিতা– যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই/যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।’) উইলফ্রিড ওয়েনের মা সুজান এইচ. ওয়েন জানতেন তাঁর ছেলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার কথা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির বাংলা তর্জমা লিপিবদ্ধ হয়েছে রথীন্দ্রনাথের ‘পিতৃস্মৃতি’ গ্রন্থে।
“শ্রজবেরি
১ আগস্ট ১৯২০
শ্রদ্ধেয় স্যার রবীন্দ্রনাথ,
যেদিন শুনেছি আপনি লন্ডনে এসেছেন, সেদিন থেকে রোজই ভাবছি আপনাকে চিঠি লিখি। আর আপনাকে আমার মনের কথাটুকু জানাবার জন্য সেই চিঠি লিখছি। এ চিঠি আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে কিনা জানি না; কারণ আপনার ঠিকানা আমার জানা নেই। তবু আমার মনে হচ্ছে লেফাফার ওপর আপনার নামটুকুই যথেষ্ট। আজ থেকে দু-বছর আগে আমার অতি স্নেহের বড়ো ছেলে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে ফ্রান্স পাড়ি দিল। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। যাবার আগে আমার কাছে বিদায় নিতে এলো। আমরা দুজনেই তাকিয়ে আছি ফ্রান্সের দিকে। মাঝখানে সমুদ্রের জল রৌদ্রে যেন ঝলমল করছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমার কবি-ছেলে তখন আপন মনে আপনার লেখা কবিতার সেই আশ্চর্য ছত্রগুলি আউড়ে চলেছে:
যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই-
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।….
তার পকেট-বই যখন আমার কাছে ফিরে এলো, দেখি, তার নিজের হাতে এই কটি কথা লিখে তার নীচে আপনার নাম লিখে রেখেছে। যদি কিছু মনে না করেন, আমায় কি জানাবেন কোন বইয়ে সম্পূর্ণ কবিতাটি পাওয়া যাবে?
এই পোড়া যুদ্ধ থামবার এক হপ্তা আগে আমার বক্ষের ধন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল, সেদিন এই নিদারুণ খবর এসে পৌঁছল আমাদের কাছে। আর কিছুদিন পরেই আমার ছেলের একটি ছোটো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে।
এ বইয়ে থাকবে যুদ্ধের বিষয়ে লেখা তার কবিতা। দেশের অধিকাংশ লোক নিশ্চিন্ত আরামে নিরাপদে দেশে বসে আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করছে, এমন-কি, প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, তাদের জন্য কোনো মমতা বা অনুভূতি নেই–এ কথা ভেবে বাছা আমার ভারি মনোবেদনা অনুভব করত। যুদ্ধে যে কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ নেই–এ বিষয়ে তার সংশয় মাত্র ছিল না। কিন্তু নিজের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে সে একটি কথাও বলেনি তার কবিতায়। যারা তাকে ভালোবাসত একমাত্র তারাই বুঝবে–কী গভীর দুঃখ ছিল তার মনের মধ্যে। তা না হলে এরকম কবিতা সে লিখতে পারত না। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ বছর। সে ছিল সৌন্দর্যের উপাসক–তার নিজের জীবন ছিল সুন্দর, কল্যাণময়। আমি অভিযোগ করব না, ভগবান তাকে যখন টেনে নিলেন, ভালোবেসেই নিয়ে গেছেন। আমার মায়ের প্রাণ, আমি নিয়ত তাঁর কাছে কত প্রার্থনাই করেছি। তিনি প্রেমময়, তিনি যদি ভালো বুঝতেন তা হলে তো মায়ের কোলেই সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। সুতরাং আমি নতমস্তকেই তাঁর বিধান মেনে নিয়েছি। যতদিন এ জগতে আছি, কোনো অভিযোগ না করে নীরবে কাটিয়ে যাব। আমাদের ত্রাণ করার জন্য যিনি মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন, তিনি আমাদের জন্য এক অমৃতলোক রচনা করে রেখেছেন। সেইখানে আমার উইলফ্রিডের সঙ্গে আমি আবার মিলিত হব। আমি যখন চিঠি লিখতে শুরু করি তখন ভাবিনি এত কথা লিখব, চিঠি বড়ো হয়ে গেল বলে আমায় মার্জনা করবেন। আপনি যদি আমার ছেলের কবিতার বইখানি পড়েন, ভারি অনুগৃহীত বোধ করব। চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস শরৎকালের মধ্যেই বইখানি বের করবে। যদি অনুমতি দেন আমি একখানি বই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।
বিষণ্ন মনের আঁধারে আলোর দিশারি মনোবিদ রবীন্দ্রনাথ
আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি,
উইলফ্রিড ওয়েনের মা
সুজান এইচ. ওয়েন”
এক পুত্রহারা মাতৃহৃদয় সান্ত্বনার সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার দিন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসোও স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি কঁতেস দ্য নোয়াইয়ের মুখে ‘গীতাঞ্জলি’র কিছু অংশ শুনে স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। এভাবেই সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মানুষের নানান মানসিক উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব–এমন কী শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সহায়ক হয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। প্রিয় বন্ধু লোকেন্দ্রনাথকে কবি লিখেছেন, “মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল প্রবন্ধের চেয়ে চিঠি বেশি উপযোগী।” সেই সব চিঠিপত্র মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথের এক স্বতন্ত্র স্বরূপ আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয়। আত্মসচেতনতা, মনের জোর, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্বাস মানুষকে যে কতখানি রোগমুক্ত করতে পারে এবং প্রতিটি কাজে উদ্দীপ্ত করে তোলে তার উজ্জ্বল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। কবির লেখা সেই সমস্ত চিঠিপত্র নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করলে আমরা খুঁজে পাই এক মনসমীক্ষক, মনোবিশ্লেষক বা মনোবিদ রবীন্দ্রনাথকে। জীবনের নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মানসিক অবসাদে ভুগেছিলেন এবং তারই পরিণতি ছিল তাঁর আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছায়। সেই সময় মানসিক অবসাদের কোনো ওষুধ ছিল না। মানসিক অবসাদ যে একটা অসুখ সে স্বীকৃতিও ছিল না। ছিল না সচেতনতাও। মনের জোর, আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা তিনি মানসিক অবসাদকে জয় করেছিলেন বারবার। অচিরেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন স্বাভাবিক জীবনে, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কর্মযজ্ঞে। কবি বুঝতেন এই পৃথিবীতে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে থাকতে গেলে নিজের কিছু ভালোলাগাবোধ বা কাজকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। সে কারণেই ছেলেবেলা থেকে বারবার অবসাদের ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিতা লেখা, গান লেখা ও গাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো ও দুর্বল মুহূর্তে নিজের একান্ত কিছু সময় নির্জনে কাটানো। প্রতিটি কাজের আত্মবিশ্লেষণ কবির মনকে সমৃদ্ধ করেছে, আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কবি তাঁর আশপাশে থাকা অসংখ্য মানুষের, প্রিয়জনের মনের দুঃখ-কষ্ট ও অবসাদ দূর করার চেষ্টা করেছেন এক অভিজ্ঞ মনোবিশ্লেষকের মতো। কবির কথা হলো–মনের দরজা খুলে দাও। সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ, প্রেম-ভালোবাসা যাই থাক মনে তা ব্যক্ত কর প্রিয়জনদের কাছে। কথা বল, চিঠিলেখার মনের মানুষ তৈরি কর, যাকে সব বলা যায়। মনের ভালোলাগা ভালোবাসার বোধগুলোকে জাগ্রত কর। নিজেকে একাত্ম কর তাদের সঙ্গে। কবি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির মাঝখানে বেঁচে থাকার আনন্দ আছে, যা আমাদের চিত্তবিকলন থেকে উত্তীর্ণ করে, অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসে। তিনি ভালোবাসতেন বর্ষার আকাশ, সজল মেঘ, পাখির কূজন, দিগন্তব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি, সোনালি রৌদ্রে নিবিড় ভাবসৌন্দর্যে ভরা দুপুর। শিমুল পলাশরাঙা আলোর ঝলকানি, গাছপালায় রোদের আলোছায়া, পুকুরে হাঁসের পাখা ঝাপটানো, শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘন বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ, শিশিরসিক্ত সুরমা সবুজের ওপর সোনা গলানো রৌদ্র। এই সবকিছুই কবির ভালোবাসা, কবির আত্মীয়, কবির অবসাদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পাথেয়। কবি ভালোবাসতেন গান, কবিতা, সমুদ্র আর নদী। অবসাদ কাটানোর জন্য ভালোবাসতেন একান্তে নির্জনবাস। শুধু নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া।
রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ছ’মাস থাকাকালীন (২৮ অক্টোবর ১৯১২ থেকে ১৪ এপ্রিল ১৯১৩) দেখা যায় কয়েকখানি পত্রে শিক্ষাসমস্যা ও তার প্রণালি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের লক্ষ্যে ও তার সঙ্গে আমেরিকার মানুষের চরিত্রগত দিকটির তুলনা করে তিনি লেখেন, ‘আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই, কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয়, কিন্তু চারি দিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে।… প্রত্যেক আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্য উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগ লাভ করবার কোনো সাধনা নেই।….মানুষের শক্তির যতদূর বড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্য সাধনা করতে হবে।’
কবি ১৯২২ সালের ১ নভেম্বর আরবানা, ইলিনয়ে বিশ্রাম নিতে যান। সেখানে তিনি ইউনিটেরিয়ানদের একটি ছোটো ক্লাবের অনুরোধে প্রথম ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হন। তার পরের তিন সপ্তাহে তিনি পাঁচবার শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা থেকে ভাষণ দেন। এই ভাষণগুলোকে ভিত্তি করে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।
কবি এরপর ইংল্যান্ড ফিরে আসেন। সেখানে কোয়েস্ট নামক এক তাত্ত্বিক পত্রিকার সম্পাদক তাঁদের সমিতির ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করেন। ১৯ মে ১৯১৩, কক্সটন হল, লন্ডন-এ তিনি যে বক্তৃতা দেন। সেখানে শ্রোতাদের জন্য প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা ছিল। প্রশান্তকুমার পাল রচিত ‘রবিজীবনী’ ষষ্ঠ খণ্ডে টিকিটের (প্রবেশ মূল্য দশ শিলিং) যে ছবিটি দেখা যায় তাতে কবির বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করা আছে ‘দ্য সার্চ ফর গড’ এবং মোট পাঁচটি বক্তৃতার তারিখ দেওয়া আছে (পৃ. ৪০২)। যদিও রবীন্দ্রনাথ ‘ছটি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।’ ‘দ্য রিয়েলাইজেশন অব ব্রাহ্ম’ বক্তৃতাটির আয়োজন করা হয় কেনসিংটন টাউন হলে। রিয়েলাইজেশন ইন অ্যাকশন শীর্ষক অতিরিক্ত প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন নটিংহিল গেটে অবস্থিত ব্রাহ্ম সমাজে….। এই প্রবন্ধটি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ‘কর্মযোগ’ থেকে অনুবাদ করে দেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ সাধনার ভূমিকায় লিখেছেন।
প্রকৃতির সঙ্গে মিলনে মানসের আত্মবোধ হয়। সে প্রকৃতির সঙ্গে দু’ভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। এক, সে প্রয়োজনের সম্পর্ক স্থাপন করে-প্রকৃতির সব নিয়ম জেনে ও তার নানাভাবে ব্যবহার করে। এই জ্ঞানলাভ করাও তার এক তপস্যা, যা তাকে করে তুলেছে আজকের উন্নত মানুষ। দুই, প্রকৃতির সঙ্গে সে এক নিত্য সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে, যখন সে আত্মিক দৃষ্টি লাভ করে। সে স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরে পৌঁছোতে দীর্ঘকাল কাটায়। তার আত্মবোধ হয়, যা তার অন্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটায়। আপন আত্মাকে জানার জন্যই তার ‘অপরাজেয় তপস্যা’ যাতে সে অন্য মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে বাধাহীন হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়।
কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ জানেন যে মানুষ জগৎ ও জীবনকে যুক্ত করে দেখেই জীবনে পূর্ণতা লাভ করে এবং এই পূর্ণতার বোধই মানুষের ঈশ্বর। ঈশ্বরও বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষ প্রেমের সম্পর্কেই মিলিত হং। প্রেম কীভাবে আত্মোপলব্ধি সম্ভব করে তার আলোচনায় জানা যায় যে সৃষ্টিতে আমরা বহু কিছুকেই দেখি পরস্পরের বিপ্রতীপে, যাকে বলা যেতে পারে দ্বন্দ্ব– যেমন ঋনাত্মক ও ধনাত্মক মেরু বা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে শক্তিগুলো বিপরীত দিকে থেকে কার্যসম্পাদন করলেও তাদের কাজে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রকৃতির মধ্যেও যে বৈপরীত্য দেখা যায় তা বিশ্বজগতে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটায় না।
সুভাষ সিংহ রায়: রাজনৈতিক বিশ্লেষক